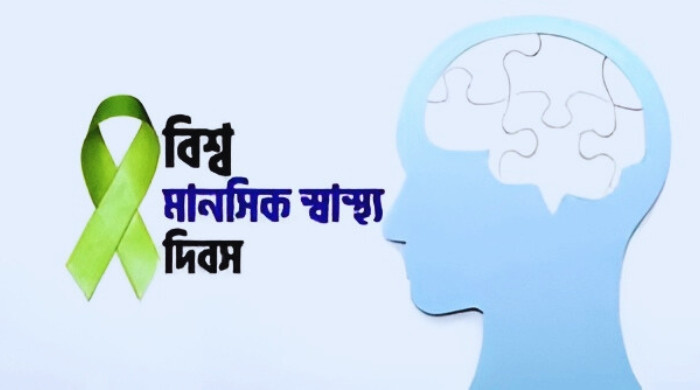ছবিঃ বিপ্লবী বার্তা
“যে জাতি তার শিক্ষকদের প্রাপ্য সম্মান দিতে পারে না, সে জাতির ভবিষ্যৎ টিকে না।” বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার দিকে তাকালে এ কথাটি যেন আর প্রবাদ নয়, বাস্তব চিত্র।
দেশজুড়ে প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষকরা আজ এক নিঃশব্দ লড়াইয়ে। কারো মুখে অভিযোগ নেই, কিন্তু চোখে ক্লান্তি স্পষ্ট—অর্থনৈতিক সংকট, অনিশ্চয়তা এবং অবমূল্যায়নের দীর্ঘ ছায়া তাদের ঘিরে রেখেছে।
বাংলাদেশে একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মাসে গড়ে প্রায় ২২,০০০ থেকে ২৬,০০০ টাকা এবং একজন কলেজ পর্যায়ের প্রভাষকের গড় বেতন ৩০,০০০–৩৫,০০০ টাকা।
অন্যদিকে, রাজধানী ঢাকায় জীবনযাত্রার ব্যয় গত ৫ বছরে বেড়েছে ৬৫%। ফলে শিক্ষকরা মাসের প্রথম সপ্তাহ পার করতেই হিমশিম খান।
নরসিংদী জেলার মনোহরদী থানার নাম প্রকাশ শর্তে অনিচ্ছুক এক প্রাথমিক শিক্ষক বলেন, “আমি দশম গ্রেডের বেতন পাই। বাচ্চার স্কুল ফি আর বাড়িভাড়া দিয়েই সব শেষ। সমাজে শিক্ষক হিসেবে সম্মান পাই, কিন্তু নিজের সন্তানকে ভালোভাবে পড়াতে পারি না — এ কেমন সম্মান?”
২০২৪-২৫ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ ছিল ৮২ হাজার কোটি টাকা, যা জিডিপির মাত্র ১.৮ শতাংশ। বিশ্ব ব্যাংকের মানদণ্ড অনুযায়ী, একটি উন্নয়নশীল দেশের জন্য ন্যূনতম ৪ থেকে ৬ শতাংশ বরাদ্দ প্রয়োজন। অর্থাৎ, বাংলাদেশে শিক্ষা খাতে ব্যয় হচ্ছে প্রস্তাবিত মানের অর্ধেকেরও কম।
বিশেষজ্ঞদের মতে, “শিক্ষার বাজেট যতই কম থাকে, শিক্ষক মর্যাদা ততই কমে। কারণ সেই বাজেট দিয়েই নির্ধারিত হয় প্রশিক্ষণ, বেতন, গবেষণা ও শিক্ষার মান।”
প্রায় সব পর্যায়েই শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম ও ঘুষের অভিযোগ দীর্ঘদিনের। বেসরকারি স্কুল, কলেজ, এমনকি কিছু সরকারি নিয়োগেও ‘অর্থের বিনিময়ে’ পদ পাওয়া এখন প্রকাশ্য গোপন সত্য।
রাজধানী ঢাকার এক বেসরকারি কলেজ শিক্ষক আমিনুল ইসলাম জানান, “আমাকে বলা হয়েছিল, চাকরি চাইলে ১০ লাখ টাকা লাগবে। আমি দিতে পারিনি, তাই বছরখানেক অপেক্ষা করতে হয়েছে। অনেকেই অর্থের বিনিময়ে নিয়োগ পেয়েছেন, কিন্তু যোগ্যতা নিয়েও নিয়োগ পাচ্ছে না বহু প্রার্থী।” এই চিত্র শুধু দুর্নীতির নয়, বরং শিক্ষার নৈতিক ভাঙনের প্রতিফলন। যেখানে অর্থই যোগ্যতার বিকল্প হয়ে উঠছে।
সারা দেশের স্কুলে ক্লাসে উপস্থিত শিক্ষক অনেক সময় অনুপস্থিত মানসিকভাবে। মোবাইলে ব্যস্ততা, নিরুৎসাহ পরিবেশ এবং প্রশাসনিক চাপের কারণে পাঠদানে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন অনেকেই। ফলাফল— শিক্ষার্থীরা হারাচ্ছে শেখার আগ্রহ ও পারস্পরিক বিশ্বাস।
রাজধানীর আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের ৮ম শ্রেণির নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষার্থী বলেন, “স্যার বই পড়ে শোনান, কিন্তু ব্যাখ্যা করেন না। প্রশ্ন করলে বলেন—‘বইয়ে তো লেখা আছে’। ক্লাস শেষ হয়, কিন্তু শেখা হয় না।”
দেশে শিক্ষা নীতি তৈরি হয় প্রশাসনিক বোর্ড ও রাজনৈতিক বিবেচনায়, কিন্তু মাঠের বাস্তবতা যারা জানেন—সেই শিক্ষকরা নীতিনির্ধারণের অংশে যুক্ত করা হয় না। ফলে সিদ্ধান্ত হয় ‘উপরে থেকে’, বাস্তব প্রয়োগ হয় না নিচে।
গবেষকদের মতে, শিক্ষককে বাদ দিয়ে শিক্ষা পরিকল্পনা করা মানে, রোগী ছাড়া ওষুধ তৈরি করা। মাঠের বাস্তবতা না জানলে নীতি হবে কাগজে, শিক্ষার্থীর জীবনে নয়।
দেশের প্রায় ৭০ শতাংশ শিক্ষক কর্মরত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে। তাদের অনেকেই পান না নির্দিষ্ট বেতন, উৎসব ভাতা, এমনকি নিয়মিত চাকরির নিশ্চয়তাও নেই। অন্যদিকে সরকারি শিক্ষকদের তুলনায় তারা বঞ্চিত পদোন্নতি ও মর্যাদায়।
নরসিংদীর জেলার পোড়াদিয়া কারিগরি মহাবিদ্যালয়ের এক কলেজ শিক্ষক জানান, “আমরা ক্লাসে পূর্ণ সময় দিই, অথচ বেতন পাই দুই মাস পরপর। উৎসব বোনাস বলতে কিছুই নেই। জীবিকা নয়, টিকে থাকা এখনই কঠিন।”
একসময় শিক্ষক মানে ছিল সমাজে শ্রদ্ধার প্রতীক। এখন তা অনেক জায়গায় কমে গেছে। কোচিং-বাণিজ্য, প্রশ্নফাঁস, ও বাণিজ্যিক শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে শিক্ষকতার ভাবমূর্তি ক্ষয়ে যাচ্ছে। যে পেশা একসময় অনুপ্রেরণার প্রতীক ছিল, তা এখন অনেকের কাছে হয়ে উঠেছে ‘শেষ বিকল্প চাকরি’।
সবকিছু সত্ত্বেও এখনো হাজারো শিক্ষক আছেন যারা নিজ অর্থে স্কুল চালান, গ্রামের মাটিতে প্রজন্ম গড়েন। কেউ পাহাড়ে, কেউ চরাঞ্চলে, কেউ শহরের বস্তিতে—তারা নীরবে শিক্ষা ছড়িয়ে দিচ্ছেন, বিনা প্রচারে। তারা প্রমাণ করছেন, শিক্ষকতা এখনো পেশা নয়, এক ধরনের সাধনা।
ইউনেস্কোর দক্ষিণ এশিয়া দপ্তর ২০২৪ সালের প্রতিবেদনে জানিয়েছে, বাংলাদেশে প্রতি ৪ জন শিক্ষকের মধ্যে ১ জন মানসিক চাপ ও আর্থিক সংকটে পড়েন নিয়মিত।
যে শিক্ষক নিজের সন্তানকে ঠিকভাবে পড়াতে পারেন না, তিনি কিভাবে জাতির সন্তানদের শিক্ষিত করবেন? যে জাতি তার শিক্ষকদের কণ্ঠ শুনতে চায় না, সেই জাতি কি সত্যিই ভবিষ্যতের দাবি রাখতে পারে?
আজ শিক্ষকরা যদি টিকে থাকার লড়াইয়ে ব্যস্ত থাকেন, তাহলে আগামী প্রজন্মের মানসিক দিকনির্দেশনা কে দেবে? সম্ভবত—এই প্রশ্নের উত্তরেই লুকিয়ে আছে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার ভবিষ্যৎ।